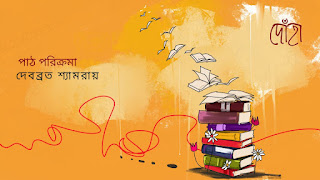 |
| প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শর্মিলী মোস্তফী |
দেবব্রত শ্যামরায়
একটি শিল্পকর্মকে ঠিক কখন উত্তীর্ণ বলা যায়? সেটি গল্প, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, চিত্রকলা, সিনেমা যাই হোক না কেন, তার মধ্যে কোন গুণটি থাকলে আমরা তাকে সার্থক শিল্প বলতে পারি? এই বুনিয়াদি প্রশ্নটিকে নিয়ে সারা পৃথিবীর শিল্পতত্ত্বে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। তত্ত্বের ঘনঘটা যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে বলা যায়, যে শিল্প সৃষ্টির সময় সৃষ্টা নিজের সময়, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রতি সৎ ও ভানহীন, অর্থাৎ ক্যানভাস ক্যামেরা বা সাদা পৃষ্ঠার সামনে সৃষ্টা যদি নিজের আত্মাকে নগ্ন করে দাঁড় করাতে পারেন, হুবহু বুনে দিতে পারেন নিজের স্বেদ রক্ত রেচন, সেই শিল্পকর্মই সৎ ও সার্থক। সেই শিল্প পাঠে পাঠক সরাসরি শিল্পীর বুকের বাঁদিকে হাত রাখতে পারেন, বুঝে নিতে পারেন শিল্পটির উৎকর্ষ ও সীমাবদ্ধতা, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অবস্থান।
স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষে, অথবা সুধায়, নীল হয়ে আছে জয়দীপ রাউতের কৃশকায় গদ্যগ্রন্থ- রাক্ষস। গদ্যগ্রন্থ না বলে 'রাক্ষস'-কে কাব্যগ্রন্থও বলা যেত বোধহয়, যদিও লেখাগুলির নির্মিত কবিতার মতো নয়, তবুও পাঠশেষে একেকটি উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠককে যে বোধে পৌঁছে দেয়, অথবা স্রেফ চুপ করে থাকতে বলে, এই বইয়ের প্রায় প্রতিটি লেখাই কমবেশি একই অনুভবে জারিত করে। কিন্তু প্রকাশক স্বয়ং, এবং বইয়ের কথামুখে কবি জয় গোস্বামী লেখাগুলিকে গদ্যই বলেছেন, তাই আমরাও, আপাতত, চেষ্টা করব একে অন্য কিছু না বলার।
অস্তিত্বের বিষে নীল হয়ে আছে জয়দীপের 'রাক্ষস'। সেই নীলের ছোঁয়া কবিকৃত মলাটেও। একটি বিবাহিত পুরুষের জীবনে দ্বিতীয় নারী, যে দীর্ঘদিন ধরে তার গোপন প্রেয়সী, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ-পরবর্তী নিদারুণ হৃদয়বেদনা - গদ্যগুলির পাঠে এমন একটি চাবি-আদল পাঠকের মনে ঘুরেফিরে উঁকি দেবে। আরও সহজ করে বললে, প্রেম ও বিরহ, বাংলা সাহিত্যের আবহমান কাব্যধারার (প্রিয় পাঠক, গদ্যগ্রন্থের তুলনায় 'কাব্য' শব্দটির প্রয়োগ আটকে রাখা গেল না) বহু-চর্চিত বহু-ব্যবহৃত এই উপাদান 'রাক্ষস'-এরও প্রধান সুর। অথচ, বাংলা কাব্যের এই প্রবহমানতার সূচনা যদি পদাবলী- কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনে উদযাপন দিয়ে হয়ে থাকে, দায়িত্ব নিয়ে বলা যেতে পারে, সেই চলমানতায় সার্থক ও শেষতম সংযোজন 'রাক্ষস'। যেকোনও উত্তীর্ণ শিল্পকর্মের ব্যর্থতাপূর্ণ সাফল্য বা সফলতাময় ব্যর্থতা এই যে তার গুণপনাকে কোনও পোলিটিকাল ইনকারেক্টনেস-এর গণ্ডি দিয়ে মাপা যায় না, যদি মাপা যেত তাহলে রাধা ও কৃষ্ণের সামাজিকভাবে অবৈধ প্রেমকাহিনি আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের যাবতীয় শিল্পস্রোতধারার উৎসমুখ হয়ে উঠতে পারত না৷ শতাধিক পৃষ্ঠার 'রাক্ষস'-এ লেখা ও আঁকায় জয়দীপ রাউত পরম বৈষ্ণবের মতোই সেই একই অমরত্বকে ছুঁতে চেয়েছেন।
আসুন, বইটি থেকে দুটো গদ্য পাঠ করা যাক। প্রথমটি নাম-গদ্য।
-----
রাক্ষস
প্রেম অনেকটা আয়নার মতন৷ একটা প্রিয় আয়না। মাঝে মাঝে যার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয় অথবা সেই আয়না আমাকে কীভাবে দেখছে সেটা বুঝে নেওয়াই প্রেম। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না "কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে, কাহারও প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে।" এই প্রেমের বেদনাটাই আসলে প্রেম। কার প্রেমের বেদনায় আমি জাগ্রত জানতে ইচ্ছে হয়েছে। জেনেছি তা। হ্যাঁ, আমার জীবনেও অতুলনীয় আর অনিয়ন্ত্রিত প্রেম এসেছে, তবে সে-প্রেম রাজকন্যা ও রাজপুত্রের প্রেম নয়। বরং সে-প্রেম রূপকথার রাক্ষস আর রাক্ষসের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা এক রাজকন্যার যেরকম প্রেম, সেইরকম।
আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যখন ফিরতাম, ঘুম ভাঙাতাম তার। তারপর চুল বেঁধে দিতাম, কাজল পরাতাম, কত যে আদর আর আতর দিতাম তার গায়। কত যে গল্প বলতাম আর সে ডাগর চোখে চেয়ে থাকত। তার চোখের আয়নায় আমাকে দেখার চেষ্টা করতাম। তাই তার কাছে যতক্ষণ থাকতাম ঘুমাতে দিতাম না তাকে। সে পলক ফেললে আমি ভয় পেতাম। আবার যখন তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতাম, ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতাম তাকে। পাছে অন্য কারো ছায়া পড়ে তার আঁখি আয়নায়।
কিন্তু সত্যিকারের রূপকথার গল্প যেমন হয়, একদিন সেরকম এক রাজপুত্র এল। সে আমার রাজকন্যাটিকে নিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে। নীল রঙের সেই ঘোড়াটাকে আমি দূর থেকে দেখেছি কিন্তু আক্রমণ করিনি। মিনতি করেছি, কেবল হাহাকার করেছি, বলেছি, "ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।" আর আমার সেই হাকারের শব্দে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে আমার সাজানো প্রাসাদ। যদি যুদ্ধ হত, আমি হেরে যেতাম। রাজকন্যার কাছেই তো রাখা ছিল আমার প্রাণ-ভ্রমরের কৌটো অথবা সে-ই তো ছিল আমার প্রাণ। আমি বাধা দিইনি। একটা নীল রঙের ঘোড়ার দুটো অদৃশ্য ডানায় ভর করে এই সুদর্শন রাজপুত্তুর যেদিন হরণ করে নিল আমার সর্বস্ব, সেইদিন আমার কথাটি ফুরোল, সেদিন থেকে আমি বাক্যহারা হলাম।
----
চুপ
একদিন জয় গোস্বামী বললেন, 'জানো তো জয়দীপ, আমায় উৎপলকুমার বসু ফোন করেছিলেন। বললেন, 'জয়, একদিন এসো, দু'জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি চুপ করে বসি।"
এমন আশ্চর্য নিমন্ত্রণের কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। এমন নীরবতার নিমন্ত্রণ কেউ করতে পারেন? যে পৃথিবীতে আমরা কথা বলার জন্য মিলিত হই, সেই মুখর পৃথিবীতে চুপ করে থাকার সাধনাই তো সবথেকে কঠিন। কথা ছাড়া বাঁচব কী করে?
অথচ যত দিন যাচ্ছে ততই যেন কথা বলবার জন ক্রমশ কমে আসছে। কমে আসছে বলবার বিষয়। বয়স হলে কি এরকমই হয়? কিন্তু এই চুপ করে থাকবার যে নিমন্ত্রণ, সেই নিমন্ত্রণ কার্ডটিও তো একেবারে ফাঁকা নয়। মাথার ভিতর, মনের ভিতরকার কথা তো কোনওদিন স্তব্ধ হওয়ার নয়। যদি উৎপলকুমার বসু, জয় গোস্বামী কিছু নাও বলেন- সেই নীরবতাও তো একরকমের ভাষার জন্ম দেয়। সেই নীরবতার অর্থ স্বাভাবিক কথাবার্তার থেকে হয়তো অনেক বেশিই বাঙ্ময়। আমি একসময় প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় জয়দার বাড়ি যেতাম। আমি অসুস্থ হলে তিনিও এসেছেন আমার বাড়িতে দু-একবার। আমরা গান নিয়ে কত কথা বলতাম। কিন্তু গান তো গাইবার বিষয়। সে গান যদি না গাওয়া হয় তখন তো তা কেবল কথাই। সব কথা যেমন গান নয়, তেমন অনেক গান কখনও-কখনও কেবল কথায় পরিণত হয়ে যায়। সেই কথা ফুরিয়ে আসে ক্রমশ। অথবা এমনও হতে পারে, নৈঃশব্দই আমাদের প্রকৃত কথার কাছে নিয়ে যায়। যদি কথা আপনি না ফুরায় তবে সাধনা করতে হয়। নিজেকেই ফোন করে বলতে হয়-- কথা তো অনেক হল, এসো নিজের মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকা যাক এইবার। অন্যের নয়, নিজের ভিতর যত কথা সব ক্রমশ চুপ হয়ে এলেই পৃথিবীর প্রকৃত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে বাঁশি বাজে, যে গান বাজে, তাকে শুনতে পাওয়া যায়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর অবিরত ঘূর্ণনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় আর নিজের মুখোমুখি নিজে অথবা অন্য যে জন, সেও সেই নীরবতা শুনে বুঝে নেয় একে অন্যের মন, যা বলে বোঝানো অসম্ভব।
জয়দীপ রাউতের 'রাক্ষস' নিজের পাশে চুপ করে বসে, নিজের কথা, কবির কথা শোনার সেই দুর্লভ আমন্ত্রণপত্র।
রাক্ষস। জয়দীপ রাউত। ইতিকথা পাবলিকেশন। কলকাতা বইমেলা ২০২২। ২০০ টাকা।


